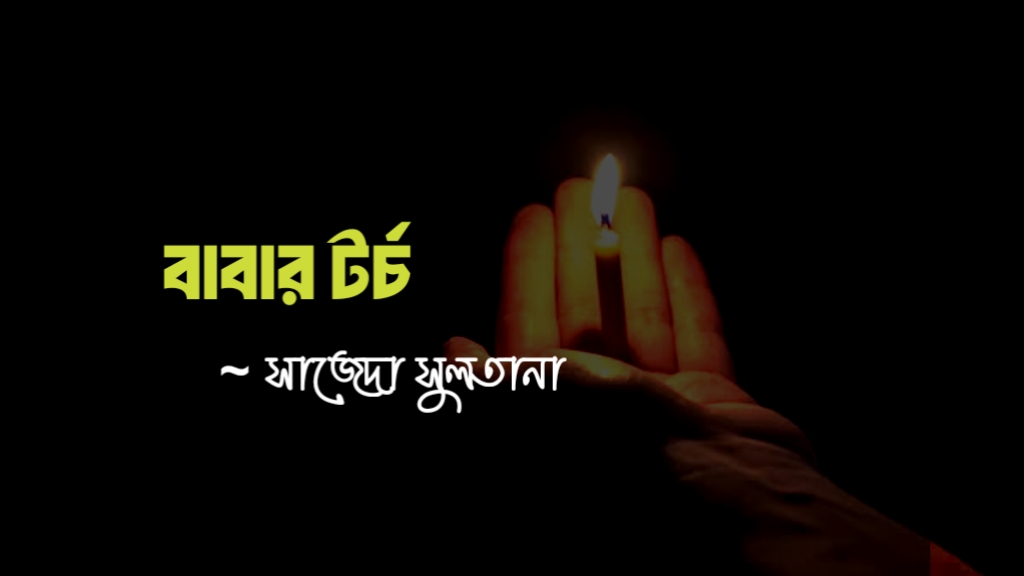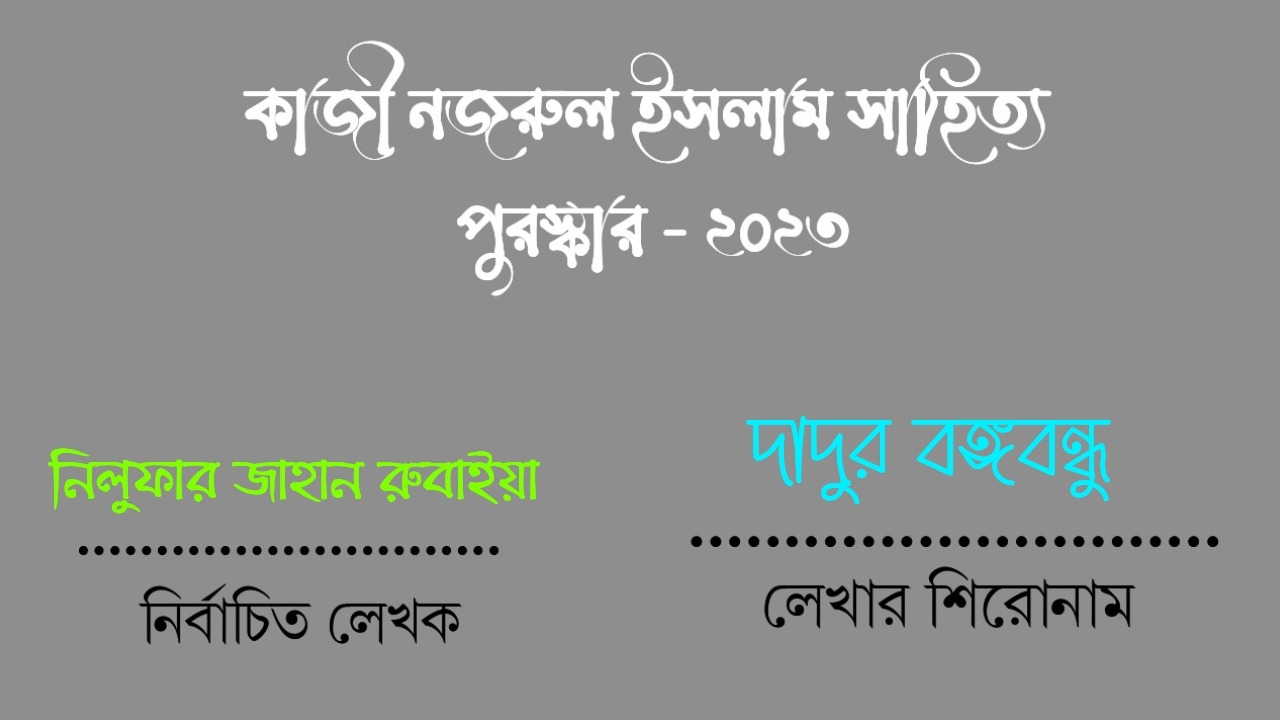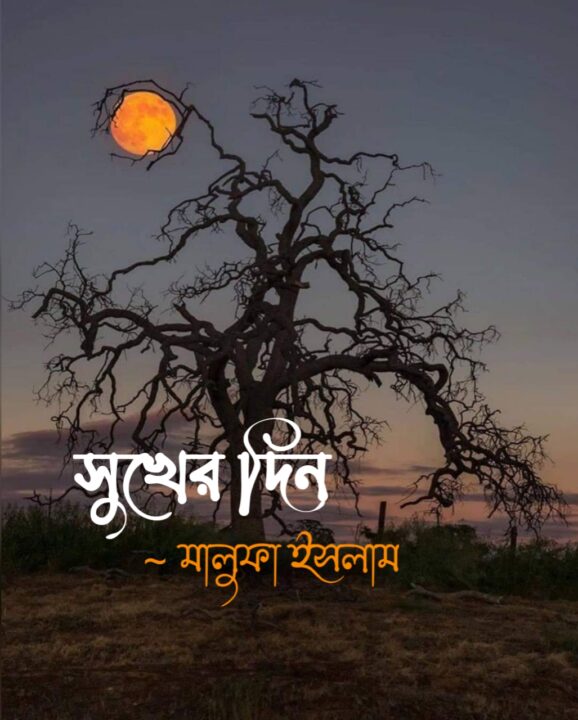বাবার টর্চ
সাজেদা সুলতানা কলি
বাবা নেই আজ তেত্রিশ বছর। দেখতে দেখতে কতগুলো বছর কেটে গেল ! মনে হচ্ছে এই সেদিন চোখের সামনে সিনেমার ফ্ল্যাশ ব্যাকের মত একের পর এক দৃশ্য ভেসে উঠছে ! আব্বা ছিলেন মা (আমার দাদু) অন্ত প্রাণ। দাদুকে ধরে ধরে বাথরুমে নেওয়া, জামা কাপড় পরিস্কার করা, খাওয়ানো সব সব কিছু করতেন নির্দিধায়। নিজের জামা কাপড় রেখে দিতেন কিন্তু দাদুর গুলো নিজ হাতে কাচতেন। মায়ের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা দেখে অনেকে তাকে বলতো দ্বিতীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। আব্বাও ছিলেন দাদুর জান প্রাণ। দাদুর দশ ছেলে মেয়ে সবার ছোট ছিল আব্বা। তারচেয়ে বড় কথা আব্বার বড় পাঁচ ভাই বোন অকালে মারা গেছেন হয়তো সেজন্য তার মধ্যে ছিল দাদুর প্রাণপাখি। এগুলো আম্মার কাছে শোনা গল্প। আমাদের বাড়ির সামনে দিঘি টাইপের একটা পুকুর আছে যেটা বড় পুকুর নামে পরিচিত।
স্কুলের ছুটির দিন গুলোতে আব্বার সাথে সাথে ঘুরতাম। বাড়ির পাশের পুকুর পাড়ে বসে বসে আব্বা আমাদের নখ কেটে দিতেন দা দিয়ে। সেটাও মোটামুটি বড় পুকুর। ঢাউস আকারের বড় বড় কতগুলো কালো পিঁপড়া খুব দ্রুত ছোটাছুটি করে। হঠাৎ হঠাৎ বিনা কারণে এরা তাদের সামনের সাঁড়াশির মত জিনিসটা দিয়ে কামড়ে ধরতো। আমি তাদেরকে কখনো মেরেছি এটা তারা কখনো বলতে পারবে না। তারপরও আমার উপর কেন আক্রোশ ছিল জানি না। আব্বার কাঁধে চড়ে বড় পুকুরের স্বচ্ছ টলটলে জলে গোসল করতে যেতাম। বাড়ি ফিরে আসার বাহন ও ছিল সেটাই। দুই ঈদের দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে আব্বা গোসল করিয়ে দিতেন। এপ্রিল মে মাসের গরম কালেও কাঁপুনি উঠে যেতো।
ছোট বেলায় আমরা হারিকেনের আলোয় লেখাপড়া করেছি। রাত দশটার পর বাড়ির কেউ তেমন আর জেগে থাকতো না তবে আমাদের ঘরে হারিকেন অনেক রাত অবধি জ্বলতো। হারিকেনের আলোয় আম্মার লেখালেখি আর আমার পাঠ্য বইয়ের আড়ালে লুকিয়ে গল্পের বই পড়া চলতো।
আব্বার একটা চার ব্যাটারির টর্চ ছিল। সামনের দিকটা বড় গোলাকার। বাড়ির সামনে থেকে সেটার আলো ঘরের জানলা গলে ভেতরে পড়তো। তাছাড়া অনেক দূর থেকে আব্বার পায়ের আঙ্গুল ফোটার শব্দ শুনতে পেতাম। আব্বার হাঁটার সময় প্রতি কদমে দু’পায়ের আঙ্গুল ফুটতো যেটাকে আমরা’মটকা’ফোটা বলি। একবার এক আত্মঘাতী টর্চের বদৌলতে সিঁদেল চোরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। তখন ছিল মাটির ভিটেয় টিনের চালের ঘর। ভদ্রলোকের টর্চের আলো ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় পড়ে সারা ঘর আলোকিত হয়ে পড়ে। আমার ‘পান খেকো’ নানু রাত দুপুরে পান সাঁজছিলেন হঠাৎ আলোর রোশনাই দেখে সবাইকে ডাকাডাকি করেন। সবাই গিয়ে দেখেন চোর সিঁদ কেটে ঢুকে শিল পাটাটা বের করে এনেছে। মানুষ জনের উপস্থিতি টের পেয়ে ততক্ষণে বাবা জীবন তার অলুক্ষনে টর্চ নিয়ে পগারপার। তার টর্চটি কয় ব্যাটারির ছিল জানা হলো না। কারণ এই গল্প আমার জন্মের আগের। নাহলে জানার চেষ্টা করতাম। এই ঘটনার পর আব্বা সিদ্ধান্ত নেন ঘর পাকা করবেন। পরদিনই ইট আনা হলো এবং ঘরের কাজ শুরু করে দিলেন। ধর তক্তা মার পেরেক অবস্থা। দাদুরও বয়স হয়েছে উনি যাতে ছোট ছেলের পাকা বাড়ি দেখে যেতে পারেন তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত দ্রুত কাজ।
পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই গ্রামের রাজমিস্ত্রীর করা নকশায় তিন তলা ফাউন্ডেশন দিয়ে আমাদের স্কুল ঘরের মতো ঘর উঠে গেল। ছাদ টাদ পিটানো শেষ। অনেক পরে দোতলায় একটা রুম করা হয় সেটার কথা আমার একটু মনে আছে। যাই হোক আমার দাদুর জীবনের শেষ দিন গুলো আমাদের পাকা ঘরেই কেটেছে। আব্বার আশা শতভাগ পূরণ হলো।
লেখালেখির সাথে যুক্ত থাকা আমার আম্মার যেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না তেমনি স্ব শিক্ষায় সুশিক্ষিত আমার আব্বারও কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। কেন ছিল না সেটা অন্য গল্প শুধু এটুকু বলে রাখি আব্বার বয়স যখন চার বছর তখন দাদা মারা যায়। তো জ্ঞান হওয়া থেকে আম্মাকে দেখে আসছি বই খাতা কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। সত্তুর আশির দশকে গ্রামের একজন গৃহবধূর দিনের বেশিরভাগ সময় কাটতো গল্পের বই পড়ে আর লেখালেখি করে। পরবর্তীতে সেই লেখা একাধিক জাতীয় দৈনিকে, সাপ্তাহিকে ছাপাও হয়। এখান থেকে বোঝা যায় যে আমার আব্বার মন মানসিকতা কতটা উঁচু পর্যায়ের ছিল। যেটা অনেক বড় বড় সার্টিফিকেট ধারীদের মধ্যে ও খুঁজে পাওয়া যায় না। বাজারের ফর্দের মধ্যে আম্মার খাতা কলমের জায়গাও থাকতো। আমাদের ঘর ভর্তি বই খাতা পত্রিকার ছড়াছড়ি ছিল। আব্বা আম্মার লেখালেখির অভ্যাসের জন্য শুধু গর্ব বোধ করতেন না উৎসাহও দিতেন যার জন্য মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আম্মাকে এস এস সি পরীক্ষা দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলন। আম্মা এই ডামাঢোলের মধ্যে শুধু মাত্র সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষা দিতে রাজি হননি।
ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার পরবর্তীতে চেয়ারম্যান হওয়া আমার আব্বা ছিলেন আগা গোড়া একজন কৃষক। তবে তাঁকে কখনো মাঠে কাজ করতে দেখিনি। ক্ষেত খামার আর গবাদি পশু দেখা শোনার জন্য দুই জন লোক সবসময়ই থাকতো। ফসলের মৌসুমে বাড়তি লোক জন রাখা হতো। গৃহস্থালি কাজে সহযোগিতার জন্যও লোক থাকতো এবং ধানের মৌসুমে আলাদা একজন মহিলা থাকতো। যার জন্য গ্রামে বড় হয়েও আমাদের শৈশব কৈশোর কেটেছে বলতে গেলে রাজার হালে।
বর্তমান সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের কথা শুনে অবাক লাগে। চেয়ারম্যান হিসেবে পাওয়া মাসিক পাঁচশো টাকা সম্মানি আব্বা অস্বচ্ছল একজন সদস্যকে দিয়ে দিতেন। যেখানে সরকারি কাজ সরকারি কর্মী বলতে লোকজন হামলে পড়ে সেখান এরকম একজন বাবার মেয়ে হয়ে আমি গর্বিত।
আমি এবং আপু কখনো আব্বার মার তো দূরের কথা বকা শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। তবে ভাইয়া কয়েকবার রাম ধমক এবং ধোলাই খেয়েছে। একবার ভাইয়া আমাদের প্রতিবেশীর গাছে অনেক আম দেখে বলেছিল, ক..ত.. আম ! আব্বা সাথে ছিলেন, ভাইয়া পুরোপুরি অবাক হওয়ার আগেই গর্জন শুনতে পেল — যত আম হোক ওদিকে তাকাতে হবে না। আমাদের ঘরের পেছনে লাগোয়া বেশ বড় এবং গভীর একটা পুকুর আছে। হালকা একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়লেই সেই পুকুরে মাছ ভেসে ওঠে। অংশীদার যারা মোটামুটি সবাই নামে মাছ ধরতে। এদিকে আমাদের তো হাত নিশপিশ করছে আব্বা কখন বাইরে যাবে তারপর নেমে পড়বো। তখন সময়টাকে অনেক লম্বা মনে হতো এদিকে ভেসে থাকা মাছগুলোও তো ডুবে যাচ্ছে। ততক্ষণে মাছ ধরতে যাওয়া সবাই গোসল সেরে উঠে পড়েছে। আরেকবার আপু সকাল বেলা ছিপ দিয়ে বড় একটা রুই মাছ ধরে ফেলে। মাছ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই আব্বার মুখোমুখি। আব্বা মুখে কিছু না বলে শুধু চোখগুলো একটু বড় করেছিলেন এতেই কাবু হয়ে আপু মাছটা সসম্মানে পুকুরে ছেড়ে আসে। কারণ পুকুরটি আমাদের একার নয়।
ভাইয়া নটরডেম কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগ নিয়ে পাশ করেছে দেখে খুশিতে আব্বার চোখে পানি চলে এসেছে। মেডিকেল এ্যাডমিশনে পঁচাত্তর নম্বর দরকার ভাইয়া পেল সত্তর। কোন এক শুভাকাঙ্ক্ষী আব্বাকে বলেছিলেন দশ হাজার (১৯৮৮ সাল) টাকা দিলে ভর্তি করে দিতে পারবেন। এস সি পরীক্ষার শেষের দিকের একদিনের কথা পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে বাড়তি বই খাতা সামনের টেবিলে জমা রাখতে হয়। ঘন্টা পড়ে গেছে আমি তখনও আমার বই জমা রাখিনি। আব্বা আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার আগে সেই চোখ গুলো একটু বড় করে তাকিয়েছেন। আমি পড়িমরি করে বইটা টেবিলে রেখে আসি।
আমাদের বন্যা প্রবণ এলাকায় প্রতি বছর কয়েক বার বন্যা হয়। সেবার (১৯৮৩) একটু বেশিই পানি হয়েছিল। বিকেলের মধ্যেই সবার ঘরে পানি ঢুকে পড়েছে। সন্ধ্যার আগেই আশেপাশের সবাই আমাদের ঘরে এসে আশ্রয় নেয় যেহেতু আমাদের ঘর মাঝখানে হয়তো মনে করেছেন পানি ঢুকবে না। তাই আব্বাই সবাই কে ডেকে এনেছেন। পরদিন সকালের মধ্যে আমাদের ঘরেও এক হাঁটু পানি। ঘর ভর্তি মানুষ তাদের মাল পত্র হাঁস মুরগি সে এক বেহাল অবস্থা। এত লোক জনের খাবার দাবারের একটা ব্যাপার আছে। এক হাঁটু পানিতে রান্না করা তো অসম্ভব। তাই সবার জন্য কিভাবে যেন মুড়ির ব্যবস্থা করা হলো। বিকাল বেলা আমাদের ঘরের সামনে নৌকা আসলো। পালাক্রমে একে একে সবাই যে যার আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলো। আমরাও মহাখুশি এই উসিলায় নানুর বাড়িতে গিয়ে বেড়াতে পারবো। কিন্তু আব্বা রাজি হলেন না। আমাদের দোতলায় এক পরিবার, আমরা এবং আমাদের সামনের ঘরে আমার জ্যাঠাতো ভাইয়ের পরিবার রয়ে গেছে। তাদের ঘরও পাকা বলে থাকতে অসুবিধা হয়নি। পুরো বাড়িতে সুনসান নিরবতা। কি করবো পড়াশোনা নেই, খেলাধুলা করার জায়গা নেই। লোকজন চলে গেলেও তাদের মাল পত্র সব রেখে গেছে। ঘরের এমন অবস্থা তার উপর নানুর বাড়ী যাওয়ার সুযোগ টা হাত ছাড়া হয়ে গেল। সব নিয়ে মনের দুঃখে সন্ধ্যা বেলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছি।
ঘুম ভাঙ্গার পর অনেক্ষণ বুঝতে পারছিলাম না কোথায় আছি। কারণ বিছানা বালিশ চাদর কিছু্ই নেই খাটের উপর শুধু পাটি পাতা। একটু পর বুঝলাম আব্বা খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করছেন। চোখ কচলে উঠে দেখি পুরো ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত চেয়ার পেতে রাখা হয়েছে। রাতের বেলা সাপ খোপের ভয়ে পানিতে হাঁটা অনিরাপদ তাই এই ব্যবস্থা। আম্মা সহ আমরা সবাই খাটের উপরেই বসা ছিলাম। আমি ভাবছিলাম খাবার কোথা থেকে আসবে ? ওমা দেখি আব্বা টর্চ জ্বালিয়ে প্লেটে প্লেটে করে খাবার আনছেন ! যেই সেই খাবার না। একেবারে গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ডিম আর খিঁচুড়ি ! মুখে দেয়ার আগে আব্বা বললেন লবন একটু কম হয়েছে। ছোট মানুষ খাবার পেলেই হলো অত শত জানি না। সারাদিন মুড়ি খাওয়ার পর ঐ আলুনি খিঁচুড়িও ছিল আমাদের কাছে অমৃত। সেদিন আমার আব্বা টিন কেটে রান্নার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং নিজের হাতে রান্নাও করেছিলেন।
আব্বা যে বছর মারা যান সে বছরই আমাদের গ্রামে ইলেকট্রিসিটি আসে। আমাদের ঘরের অয়্যারিংও আব্বা করে যান। কিন্তু সংযোগ দেখে যেতে পারেননি।
আব্বা আমাদের বাড়ির সামনে একটা মক্তব করেন এবং যে বড় পুকুরে আমরা গোসল করতে যেতাম সেখানে একটা পাকা ঘাট করেন। তখন রোজা হতো জুন জুলাই মাসের প্রচন্ড গরমের সময়। আমাদের ঘর মাঝখানে হওয়াতে এক ফোঁটা বাতাসও ঘরে ঢুকতো না। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে আব্বা ভোর রাতে সেহেরি খাওয়ার পর একটা বালিশ নিয়ে বড় পুকুরের সেই পাকা ঘাটের বসার আসনটাতে গিয়ে ঘুমাতেন। বেলা উঠলে আবার বাড়ি ফিরে আসতেন। কিন্তু আসনটা লম্বা হলেও পাশে একটু সরু হওয়ায় খুব একটা আরাম পেতেন না। পরবর্তীতে পূর্ব পাশের আসনটার সাথে সংযুক্ত করে চওড়া একটা বেদী তৈরি করে নেন। পরের বছরই রোজার কিছুদিন আগে পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৯০ সালের ১২ মার্চ আমার আব্বা চলে যান। আমার সবচেয়ে বেশি কষ্টের স্মৃতি সেই বেদীটা।তার উপর চোখ পড়তেই ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে উঠতো। কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা তৈরি করিয়েছিলেন সেটা উপভোগ করতে পারেন নি। আমি ২০১৬ সালে সর্বশেষ আমাদের বাড়িতে যাই। মক্তব, পুকুরের পাকা ঘাট সবই ঠিকঠাক আছে শুধু সেই বেদীটার কোন চিহ্ন দেখিনি। সেটা ঘাটলার সাথে পরে সংযোজন করাতে আলগা হয়ে খুলে চলে আসছে।
বাড়ি ফিরতে আব্বার যত রাতই হতো গোয়াল ঘরের গরুগুলো না দেখে বাড়িতে ঢুকতেন না। ততক্ষণে গরু দেখা শোনা করার লোক জন ঘুমে কাদা। সেই টর্চ জ্বেলে জ্বেলে দেখতেন গরুর খাবার দাবার ঠিক মতো দেয়া হয়েছে কিনা ঘরটা পরিস্কার করা হয়েছে কিনা। তারপর বাড়িতে ঢুকে পুরো বাড়ির আনাচে কানাচে টর্চ দিয়ে দেখে ঘরে ঢুকতেন। কখনো এই রুটিনের ব্যাত্যয় হতো না। আব্বা মারা যাওয়ার পরও চার ব্যাটারির টর্চটা অনেক দিন ছিল। চার্জ লাইটের আগমনে ব্যাটারির লাইটের আবেদন কমতে কমতে এখন বিলুপ্ত। তবে আমার এখনও মনে পড়ে স্টিল বডির টর্চটাতে কিভাবে সারিবদ্ধভাবে অলিম্পিক ব্যাটারিগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আলো জ্বালতো।